# গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশের প্রশ্নে নতুন আলোচনায় আশরাফ উদ্দিন রিজু ইস্যু # নেপথ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ঈর্ষাপরায়ণ ও স্বার্থান্বেষী মহলের দুরভিসন্ধিমূলক জিঘাংসা # বিভ্রান্তিকর প্রচার, রাজনৈতিক প্রভাব ও প্রশাসনিক নীতির দ্বন্দ্ব #
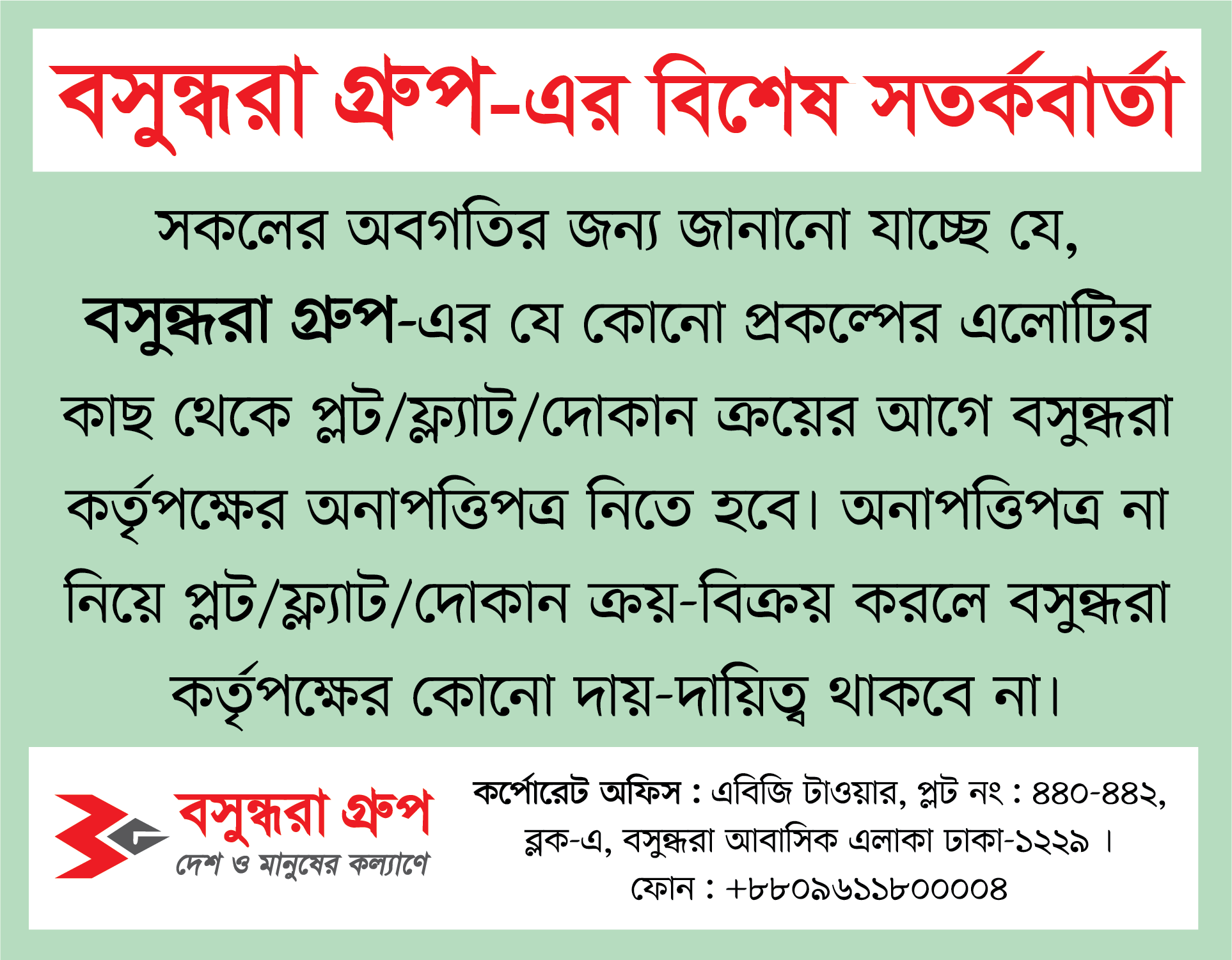

বিশেষ প্রতিবেদক : সাম্প্রতিক সময়ে সরকারি কর্মকর্তা মোঃ আশরাফ উদ্দিন রিজু, নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর তার বিরুদ্ধে প্রকাশিত একাধিক অনলাইন প্রচার মাধ্যমে প্রতিবেদনের সূত্র ধরে “ডিজিটাল সাংবাদিকতার নৈতিকতা ও দায়বদ্ধতা” নতুন করে আলোচনায় এসেছে। কতিপয় অনলাইন নিউজ পোর্টালে তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি, রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা ও টেন্ডারবাণিজ্যের বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। কিন্তু প্রতিবেদনে প্রমাণ, দলিল বা মন্তব্য উহ্য ছিল । ঘটনাটি কেবলই যে একজন কর্মকর্তার মানহানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ তা কিন্তু নয়, বরং এটি বাংলাদেশের সাংবাদিকতার একটি বড়ধরনের সংকটকেই সামনে এনেছে।
ঘটনার প্রেক্ষাপট : বিভ্রান্তিকর সংবাদ ও প্রশাসনিক বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত হয় না। চলতি বছরের ১৯ থেকে ২৬ জুলাই, এর মধ্যে একাধিক অনলাইন গণমাধ্যমে একযোগে রিজুর নামে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। শিরোনামগুলো ছিল প্রায় অভিন্ন “টেন্ডার বাণিজ্যে ছাত্রলীগেই আস্থা”, “ফ্যাসিস্টের দোসর”, “কোটিপতি নির্বাহী প্রকৌশলী” ইত্যাদি ইত্যাদি।
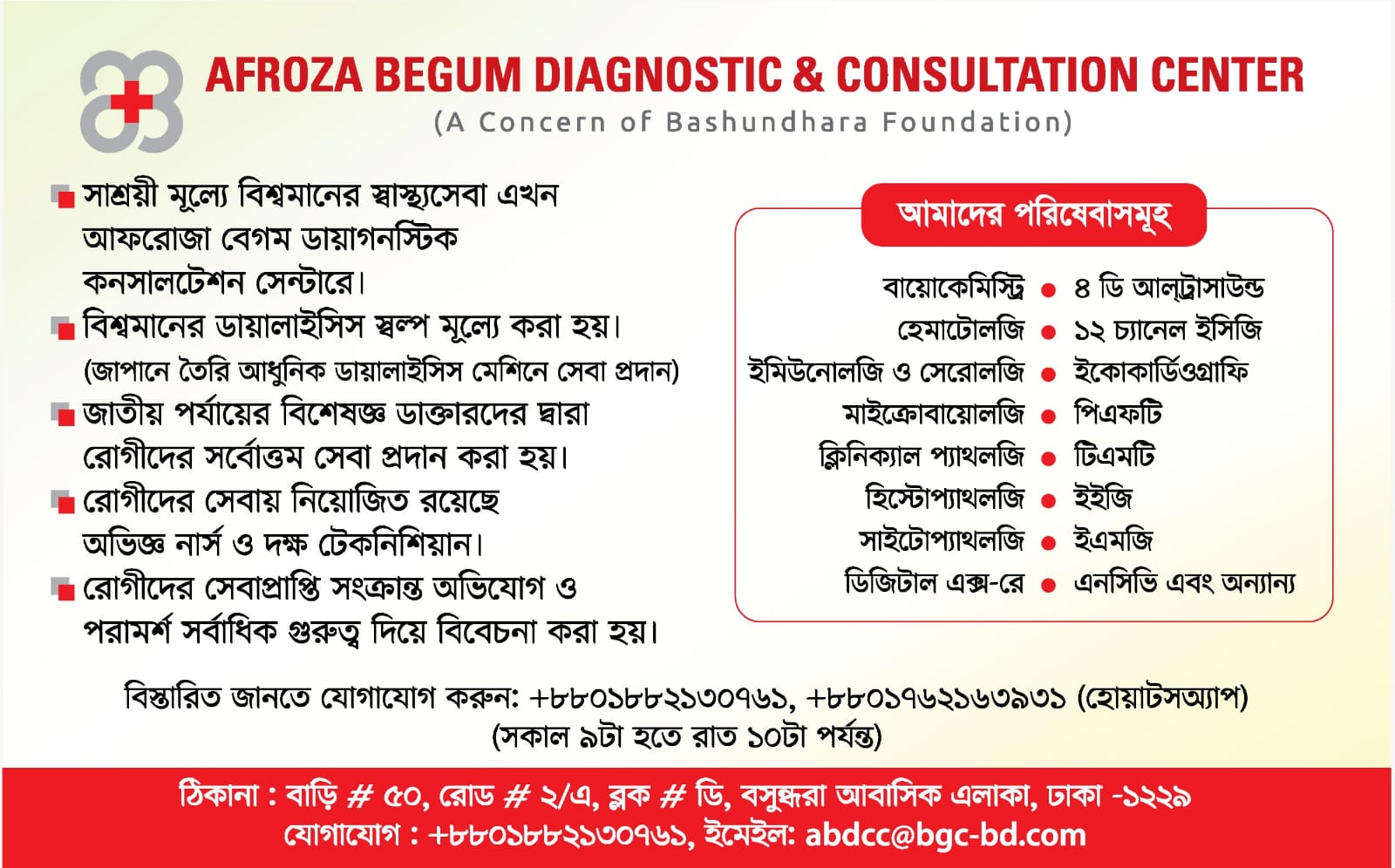
এই ঘটনাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রায় একই সময়সীমায়, প্রায় একই শব্দচয়ন এবং কোনো তথ্য প্রমাণ ছাড়া প্রায় একধরনের সমন্বিত প্রচারণার ছাপ রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি একটি coordinated smear campaign, যা রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য থেকে চালানো হয়ে থাকতে পারে।

অভিযোগ ও তথ্য যাচাইঃ যুক্তির সঙ্গে অসঙ্গতি বিশ্লেষণে দেখা যায়, তার বিরুদ্ধে মোট ৯টি অভিযোগ সংবাদে তুলে ধরা হয়। অধিকাংশ অভিযোগই বাস্তবতা ও সময়কাল অনুযায়ী অসঙ্গত।
অভিযোগ ১: তিনি কুয়েট ছাত্রলীগের নেতা ছিলেন।
কিন্তু কুয়েট ২০০৩ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত রাজনীতিমুক্ত ছিল; ছাত্ররাজনীতি শুরু হয় ২০০৯ সালে।
অভিযোগ ২: ২০০ নম্বরের পরীক্ষায় ক্যাডার হয়েছেন।
বাস্তবে ৩২তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি ছিল ১০০ নম্বরের, লিখিত ও মৌখিক মিলিয়ে ১১০০ নম্বর।
অভিযোগ ৩ : মন্ত্রীকে ঘুষ দিয়ে পোস্টিং নিয়েছেন।
ওবায়দুল মুক্তাদির মন্ত্রীর দায়িত্ব নেন ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে, আর তার পদায়ন হয় ২০২৩ সালের নভেম্বরে দুই মাস আগে।
এই তিনটি তথ্যই সংবাদে উপেক্ষিত হয়েছে, যা “information integrity”এর ঘাটতি নির্দেশ করে।
মিথ্যা প্রচারণার মনস্তত্ত্ব: পেশাগত ঈর্ষা না রাজনৈতিক ফ্যাক্টর ? : একজন কর্মকর্তা যখন প্রশাসনিক কাঠামোর ভেতরে সততার জন্য পরিচিত হন, তখন তার বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা দুই কারণে চালানো হয়, পেশাগত ঈর্ষা: পদায়ন, টেন্ডার বা অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতায় ক্ষুব্ধ অংশের প্রতিক্রিয়া। রাজনৈতিক পক্ষপাত : অতীত রাজনৈতিক পরিবেশে নিরপেক্ষ কর্মকর্তা হওয়াও অনেক সময় ‘অপরাধ’ হিসেবে গণ্য হয়।
এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, তিনি একাধিকবার বিভিন্ন জেলায় বদলি হয়েছেন এবং নিয়মভঙ্গ বা অনিয়মের কোনো অভিযোগ তার বিরুদ্ধে প্রমাণিত হয়নি। তবু তার বিরুদ্ধে ‘ছাত্রলীগ’, ‘ঘুষ’, ‘টেন্ডার সিন্ডিকেট’ এই তিন শব্দকে কেন্দ্র করে একক ন্যারেটিভ তৈরি করা হয়েছে। এটি বাংলাদেশের অনেক সৎ সরকারি কর্মকর্তার অভিজ্ঞতার সঙ্গেই মিলে যায় যেখানে “নিরপেক্ষতা”কেই সন্দেহের চোখে দেখা হয়।
ডিজিটাল সাংবাদিকতার দায় ও যাচাইহীন প্রতিবেদন ও তার পরিণতি : এই ঘটনা বাংলাদেশের অনলাইন মিডিয়া খাতের এক মৌলিক সমস্যা তুলে ধরেছে fact verificationএর অভাব। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ৪ হাজারের বেশি ওয়েবসাইট “নিউজ পোর্টাল” নামে পরিচালিত হয়, যার বড় অংশই নিবন্ধনহীন বা সম্পাদকীয় তদারকি ছাড়াই পরিচালিত। বিশ্লেষকরা বলছেন, এই অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে সংবাদ হয়ে উঠছে মতপ্রকাশের ছদ্মবেশে ব্যক্তিগত আক্রমণের অস্ত্র। ফলে ভুয়া তথ্য ছড়ানোর পর তার প্রতিকার পেতে দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়া পার করতে হয় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে যা অনেক সময় পেশাগতভাবে অপ্রতুল প্রতিরোধ হিসেবে দেখা দেয়।
আইন ও নৈতিকতার প্রশ্ন ? ব্যক্তির সম্মান বনাম সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা : বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হলেও, একই সঙ্গে বলা আছে এই স্বাধীনতা “নৈতিকতা ও জনশৃঙ্খলা”র সীমার মধ্যে। অন্যদিকে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন (DSA) অনুযায়ী, মিথ্যা বা মানহানিকর তথ্য প্রচার শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তবে সমস্যা হলো, “সত্য যাচাইয়ের দায়” কার? সাংবাদিকের? সম্পাদকীয় নীতিমালার? নাকি সরকারের নিয়ন্ত্রক সংস্থার? রিজু ইস্যু এই প্রশ্নটিকেই সামনে এনেছে নতুন করে।
প্রভাব : ব্যক্তি থেকে প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত আস্থার সংকট
এই ঘটনায় একজন কর্মকর্তা যেমন ব্যক্তিগতভাবে মানহানির শিকার হয়েছেন, তেমনি প্রশাসনিক আস্থাও আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। যখন একজন সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রমাণবিহীন তথ্য ভাইরাল হয়, তখন পুরো প্রশাসনের বিশ্বাসযোগ্যতাই প্রশ্নের মুখে পড়ে। এটি শুধুমাত্র একটি ব্যক্তির বিষয় নয় এটি প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা ও নাগরিক আস্থার বিষয়।
সত্যতা যাচাইবিহীন সংবাদ কেবল ব্যক্তি নয়, সমাজকেও বিপন্ন করে, তার ঘটনা আমাদের মনে করিয়ে দেয় ডিজিটাল সংবাদ যুগে তথ্য প্রচারের গতি বেড়েছে, কিন্তু সত্য যাচাইয়ের গতি কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে। একজন সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রমাণবিহীন অপপ্রচার কেবল তার মানহানিই নয়, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি জনগণের বিশ্বাসকেও ক্ষয় করে।
এখন প্রশ্ন আমরা কি এমন এক গণমাধ্যম সংস্কৃতি চাই, যেখানে “সত্য” হারিয়ে যাবে “শিরোনামের নাটকে”? নাকি আমরা এমন সাংবাদিকতা চাই, যেখানে বিভ্রান্তিকর সংবাদ নয়, বরং পর্যাপ্ত অনুসন্ধান, দায়িত্বশীল তথ্য সংবলিত সাবলীল ভাষায় সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠতা থাকবে সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে।
